![আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী [রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু]র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান](https://www.anjumantrust.org/wp-content/uploads/2022/08/02.-Safar.jpg)
আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী [রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু]র ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন- মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
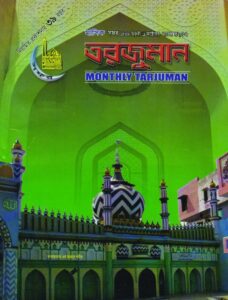 আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী
আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী
[রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু]র
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
=====
বিভিন্ন চিন্তাধারা ও মতবাদের ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনও আ’লা হযরতকে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে নাড়া দিয়েছিলো। বস্তুত তাঁর জীবদ্দশার সময়টুকু ছিলো উত্তপ্ত অবস্থা ও ঘটনাবহুল। তাঁর জন্মের পূর্বে ও পরে, তাঁর জীবদ্দশায় ও ইনতিক্বালের পর অব্যাহতভাবে বিভিন্ন আন্দোলন হতে থাকে; ঘটনা ও দুর্ঘটনা সংঘটিত হতে থাকে। যেমন, তাঁর জন্মের পূর্বে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের ওহাবী আন্দোলন ও বালাকোট আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছিলো। তাঁর জন্মের এক বছর পর ১৮৫৭ ইংরেজিতে ‘সিপাহী বিপ্লব’ সংঘটিত হয়েছিলো। তারপর ‘ইসলামী বিশ্ব ঐক্য আন্দোলন’ সংঘটিত হলো। এর সাথে সাথে দেওবন্দ আন্দোলন, আলীগড় আন্দোলন, নাদ্ওয়াতুল ওলামা আন্দোলন ও ক্বাদিয়ানী আন্দোলন চলতে লাগলো। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ’ প্রতিষ্ঠিত হলো। ‘রেশমী রুমাল আন্দোলন’ চললো। ত্রিপলী ও বলক্বান যুদ্ধ, তারপর বিশ্ব যুদ্ধ হলো। তারপর ‘খেলাফত আন্দোলন’, ‘অসহযোগ আন্দোলন’ চলতে লাগলো। এগুলোর সাথে সাথে স্বদেশ ত্যাগ আন্দোলন, গাভী যবেহ বর্জন আন্দোলন, পশু বর্জন আন্দোলন, খদ্দর আন্দোলনও চললো একের পর এক। এ সময়ে ‘জমিয়তে ওলামা-ই হিন্দ’ কায়েম হলো।
মোটকথা, আ’লা হযরত ফাযেলে বেরলভীর পবিত্র জীবদ্দশাটুকুতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্দোলনে সরগরম দেখা যায়।
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব নজদী আ’লা হযরতের শুভ জন্মের প্রায় দেড়শ’ বছর পূর্বে নজদের আয়নিয়ায় ১১১৫ হিজরিতে (১৭০৩ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করে এবং ৯০ বছর বয়সে ১২০৭ হিজরিতে (১৭৯২খ্রি.) মৃত্যুবরণ করে। তার ‘তাওহীদ-আন্দোলন’ আরব ব-দ্বীপ এবং পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের উপরও প্রভাব ফেলেছিলো। তথাকথিত তাওহীদকে পুনর্জীবিত করা ও তাঁর ভাষায় বিদ্‘আতগুলোর মূলোৎপাটনই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য বলে দাবী করা হচ্ছিলো।
অথচ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনে তায়মিয়া দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে সা‘ঊদ (দর‘ইয়ার আমীর)-এর সামরিক মদদপুষ্ট হয়ে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব তার আন্দোলনের সূচনা করেছিলো। আর ‘কিতাবুত্ তাওহীদ’ লিখে তার ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো প্রচার করতে লাগলো।
তার ‘হায়াতুন্নবী’তে বিশ্বাস ছিলোনা। হুযূর-ই আক্রামের রওযা-ই আক্বদাসে হাযির হওয়ার মতো পুণ্যময় কাজকে হারাম বলে মনে করতে লাগলো। অনুরূপ, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহর ওলীগণের ওসীলা নিয়ে আল্লাহর সাহায্য চাওয়াকে হারাম মনে করতে লাগলো। আল্লাহর ওলীগণকে সম্মান করা এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলার নৈকট্য হাসিল করা তাদের মতে অবৈধ ছিলো। মাযারের উপর ঘর নির্মাণ ও গম্বুজ তৈরী, ফাতিহাখানির জন্য হাযির হওয়া, গিলাফ ও ফুল ইত্যাদি দেওয়া তাদের মতে হারাম ছিলো। ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব এসব কাজকে যারা সমর্থন করে তাদেরকে কাফির-মুশরিক বলে ধারণা করতো। তাদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল মনে করতো। এমনকি তার এ আন্দোলন চালানোর সময় আলেম ওলামাসহ হাজারো মুসলমানকে শহীদ করা হয়েছিলো। সাহাবা-ই কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারগুলোর উপর নির্মিত গম্বুজগুলোকে ধূলিস্যাৎ করা হলো। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী এসব ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী। সুতরাং ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের এ আন্দোলন মুসলিম বিশ্বে ও বরেণ্য মণীষীদের দৃষ্টিতে ভালো বলে বিবেচিত হয়নি। এমনকি দেওবন্দের আলিমগণও, যারা কোনো কোনো বিষয়ে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের সমর্থক, তারাও মুসলমানদেরকে কাফির বলা ও গণহত্যার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।
বাহ্যিকভাবে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব তার আন্দোলনের উদ্দেশ্যের পক্ষে যতই সাফাই বর্ণনা করুক না কেন, কিন্তু তজ্জন্য সে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলো, তা সত্যপন্থী আহলে সুন্নাত মোটেই সমর্থন করতে পারেন না বরং তাদের বিরোধিতা করাই সমীচীন।
আ’লা হযরত আল্লাহর মুহাব্বত (ভালবাসা) ও আল্লাহর ওলীগণের ভালবাসাকে ঈমানের বাহার বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। বস্তুত এটাই সঠিক। তাঁর মতে মানুষের হৃদয়-মন থেকে রসূলে আক্রামের সম্মান ও মহত্ব মুছে যাওয়া এবং ‘সলফে সালেহীন’ (দ্বীনের অগ্রণীগণ)-এর প্রতি মুসলিম জাতির ধারণা খারাপ হয়ে যাওয়া এক মহাবিপদ ও দুঃখজনকই ছিলো। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার হামফ্রে, যে ইসলামী দেশগুলোতে অবস্থান করে আরবী, তুর্কি ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলো, মুসলমান আলিমের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো এবং এ গর্হিত কাজটির জন্যই নিয়োগপ্রপ্ত ছিলো যেন মুসলমানদের হৃদয়-মন থেকে এ মহত্বটি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। কেননা, মুসলিম মিল্লাতের ক্ষমতার রহস্য এরই মধ্যে নিহিত ছিলো। আবুল হাসান আলী নদভীও (নুকূশ, লাহোর) ইসলামী বিশ্বের অবস্থাদির গভীর পর্যালোচনা করে আমাদের মধ্যে সংক্রমিত ব্যাধিগুলোর চিকিৎসা ও আরোগ্য লাভের জন্য এ নুস্খাটুকুই নির্ণয় করেছেন যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মন উজাড় করা এবং নিজেদের প্রাণ ও যাবতীয় ধন-সম্পদের বিনিময়ে ভালবাসার বিকল্প নেই। হামফ্রে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবকে দিয়ে তার এ উদ্দেশ্যকেই চরিতার্থ করেছিলো। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে, ‘বালাকোট আন্দোলনে’ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের আন্দোলনের ঝলকই দৃষ্টিগোচর হয়। বালাকোট আন্দোলন (১৮২৬-১৮৩১খ্রি.)-এর নেতা ছিলো সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী এবং তার অন্তরঙ্গ বন্ধু মৌলভী ইসমাইল দেহলভী (শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর পৌত্র); কিন্তু তাদের চিন্তাধারা ও কর্মকান্ডে শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি সন্তুষ্ট ছিলেন না।
মৌলভী ইসমাঈল ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাবের ‘কিতাবুত্ তাওহীদ’-এর আদলে ‘তাক্বভিয়াতুল ঈমান’ নামে একটি পুস্তক লিখলো। (যার বিষয়বস্তুগুলো ওলামা-ই আহলে সুন্নাত তথা সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে দারুন অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিলো।) তারপর এ ‘তাক্বভিয়াতুল ঈমান’ পুস্তকটার বহুলভাবে প্রচারের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো হলো। বালাকোট আন্দোলনের সময় যখন সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী ও মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পৌঁছলো, তখন মৌলভী ইসমাঈল সৈয়্যদ আহমদ বেরলভীর ‘ইমামতে কুবরা’ (মহান ইমাম বলে) ঘোষণা করে দিলো। আর বললো, ‘যে ব্যক্তি সৈয়্যদ আহমদকে ইমাম মানতে অস্বীকার করবে, তার রক্ত ও সম্পদ (ছিনিয়ে নেওয়া) হালাল। সুতরাং যারা সৈয়্যদ আহমদ ও ইসমাঈল দেহলভীর সাথে বিরোধ করেছেন, তাঁদের সাথে তারা যুদ্ধ করলো।
বলাবাহুল্য, মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী তার ‘তাক্বভিয়াতুল ঈমান’-এ যেসব ভ্রান্ত আক্বীদা ও ভুল চিন্তাধারা প্রকাশ করেছিলো, আ’লা হযরত বেরলভী সেগুলোর খন্ডন করলেন। আর ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী ও মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর পিছু ধাওয়া করলেন। ওদিকে দেওবন্দের আলিমগণ ‘বালাকোট আন্দোলন’কে গুরুত্বের সাথে দেখতেন। কিন্তু মৌলভী হোসাঈন আহমদ মাদানী এ আন্দোলনকে ‘মাতৃভূমির আযাদী আন্দোলন’ সাব্যস্ত করেছেন; কেননা, তাতে হিন্দুরাও অংশগ্রহণ করেছিলো।
বালাকোট আন্দোলনের পরিসমাপ্তির (১৮৩১খ্রি.) কয়েকবছর পর আফগানিস্তান/ইরানের হানাফী ঘরানার জামাল উদ্দীন আফগানী (১২৫৪হি./১৮৩৮-৩৯)-এ জন্ম গ্রহণ করলেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণী লোক ছিলেন। আফগানিস্তানে ‘মন্ত্রী’ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মিশর এবং তুরস্কও সফর করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের ফ্রি-মিশনের সাথে জড়িত ছিলেন। তারপর সেটার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৭৯খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্তানের হায়দারাবাদ ও কলিকাতায় আসেন। প্যারিস, লন্ডন, রাশিয়া ও জার্মানীতে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ সময়টুকু কনস্টান্টিনিপোলে (তুরস্ক) অতিবাহিত করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সেখানেই মারা যান। পরবর্তীতে তার তাবূত (কফিন) ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক থেকে আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।
জামাল উদ্দিন আফগানী ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, সৈয়্যদ আহমদ বেরলভী ও মৌলভী ইসমাঈলের মতো তাওহীদের উপর জোর দিতেন। তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকে নাস্তিক্য ও বস্তুবাদিতার উপর প্রাধান্য দিতেন। পশ্চিমা সংস্কৃতির মোকাবেলায় প্রাচ্য সংস্কৃতিকে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে অবিচ্ছেদ্যতার উপর জোর দিতেন। আর বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাকেই অপরিহার্য মনে করতেন।
জামাল উদ্দিন আফগানী আ’লা হযরতের সমসাময়িক ছিলেন। যখন তিনি হিন্দুস্তান এসেছিলেন, তখন আ’লা হযরতের যৌবনকাল ছিলো। আ’লা হযরত ও জামাল উদ্দিনের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্যটুকু এ ছিলো যে, এক্ষুণি উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামাল উদ্দিন আফগানী শুধু তাওহীদের উপর জোর দিতেন, আর আ’লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ‘তাওহীদ’-এর ধ্যান-ধারণার উপর জোরতো দিতেনই, তৎসঙ্গে তিনি হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহত্বের অনুভূতিকে জরুরী এবং অপরিহার্য বলে মনে করতেন। এভাবে ইসলাম ও বিজ্ঞানের অঙ্গাঙ্গিতার ব্যাপারে আ’লা হযরত মনে করতেন যে, বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও দর্শনীয় বিষয়গুলোর আলোকে ইসলামী চিন্তা-চেতনাগুলোকে যাচাই করা যাবে না; বরং ক্বোরআনী আয়াতগুলোর আলোকে বিজ্ঞানকে যাচাই করা হবে। কেননা, বিজ্ঞান হচ্ছে উন্নয়নকামী বিষয়; সেটা যত উন্নতি করবে তত সেটার অবস্থা ও সিদ্ধান্ত পাল্টাতে থাকবে; কিন্তু ক্বোরআনী আয়াতগুলো নিশ্চিত ও অকাট্য। নিশ্চিত ও অকাট্য বিষয়গুলোকে ধারণাপ্রসূত ও পরিবর্তনশীল বিষয়াদির আলোকে যাচাই করা যেতে পারে না।
আ’লা হযরত ইসলামের অকাট্যতা ও পূর্ণাঙ্গতার প্রচারক ছিলেন। তিনি প্রাচ্যের সভ্যতাকে সর্বাবস্থায় পশ্চিমা সভ্যতার উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁদের পরিবেশ ও বসবাসের নিয়মকানুন সম্পর্কে পশ্চিমারা অবগত ছিলোনা; যখন অনেক পশ্চিমা সমালোচক পশ্চিমা দেশ ও জাতিগুলোর রঙ্গে রঞ্জিত ছিলো।
দেওবন্দ আন্দোলনকে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব আন্দোলন, মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী আন্দোলন এবং জামাল উদ্দিন আফগানী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত মনে হয়। কারণ, এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে ব্যাপকভাবে ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব ও মৌলভী ইসমাঈলের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার সমর্থক হিসেবে দেখা যায়। আ’লা হযরত এ তিন পক্ষকে একই দলের মধ্যে গণনা করেন।
এভাবে আ’লা হযরতের যুগে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ দু’টি দলে পরিচিত হন- একদল বেরলভী ও অপর দল দেওবন্দী। বেরলভীগণ আ’লা হযরতকে ইমাম হিসেবে মান্য করেন আর দেওবন্দীদের নেতা ছিলেন মৌং মুহাম্মদ ক্বাসেম নানুতভী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, বেরলভী ও দেওবন্দী উভয়ের শীর্ষস্থানীয়দের হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান লাভের সনদ (সূত্র) শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তাও নি¤œরূপ-
আ’লা হযরত বেরলভী হাদীসের সনদ লাভ করেছেন শাহ্ আ-লে রসূল মারহারাভী থেকে, তিনি শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে, তিনি তাঁর পিতা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে।
দ্বিতীয়ত, মৌং মুহাম্মদ ক্বাসেম নানূতভী মৌং মামলূক আলী থেকে সনদ লাভ করেছেন, তিনি মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী থেকে, তিনি শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে আর তিনি তাঁর পিতা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে হাদীসের সনদ হাসিল করেছেন।
উল্লেখ্য, ‘দারুল উলূম দেওবন্দ’ ১২৮৩হি/১৮৬৭খ্রি. দেওবন্দের এক মসজিদে আনার গাছের নিচে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। মৌং মাহমূদ হাসান সেটার প্রথম ছাত্র ছিলেন। আর মৌং মুহাম্মদ ক্বাসেম নানূতভী ছিলেন প্রথম পৃষ্ঠপোষক। মৌং ক্বাসেমের মৃত্যু (১২৯৭হি./১৮৮০খ্রি.)-এর পর ১৮৮০খ্রি. থেকে ১৯০৫খ্রি. পর্যন্ত মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী পৃষ্ঠপোষকতা করেন। উভয়ে হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কীর হাতে ত্বরীক্বতের বায়‘আত গ্রহণ করেছিলেন। মৌং আশরাফ আলী থানভী ১৮৮০খ্রি. দেওবন্দ মাদরাসায় ভর্তি হন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে মৌং মাহ্মূদ হাসান, মৌং আবদুল আলী ও মৌং এয়াক্বূব আলী প্রমুখ ছিলেন। দেওবন্দের ওস্তাদদের মধ্যে মৌং খলীল আহমদ আম্বেঠভীও ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে ‘মাজাহিরুল উলূম’ সাহারানপুর চলে গিয়েছিলেন, যা ১৮৮৩খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।
আরো উল্লেখ্য যে, দেওবন্দী আলিমগণ ও বেরলভী আলিমগণ উভয়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হলেও ইসলামের আসল রূপরেখা ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’-এর আক্বাইদের মধ্যে উভয় পক্ষের মৌলিক বিরোধ ছিলো। এ বিরোধ প্রাথমিকভাবে তেমন দেখা না গেলেও পরবর্তীতে একেবারে সুস্পষ্ট ও কঠোর রূপ ধারণ করেছিলো। তখন এ দু’ দলের একটির দলনেতা মৌং আবদুল আলী (মৃ. ১১৪৪হি./১৮৩৫খ্রি.) ছিলেন, আর আহলে সুন্নাতের দলপতি হলেন মাওলানা ফদ্বলে রসূল বদায়ূনী (ওফাত-১২৮৯হি./১৮৭২খ্রি.)।
এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, দেওবন্দী আলিমগণ প্রত্যেক প্রকারের বিদ্‘আত (নব আবিস্কৃত বিষয়)কে পথভ্রষ্টতা মনে করতে লাগলেন, আর আ’লা হযরত শুধু ওইসব বিদ্‘আত তথা নব প্রচলিত বিষয়কে গোমরাহী (পথভ্রষ্টতা) মনে করতেন, যেগুলো শরীয়তের কোন দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর অন্যান্য বিষয়, যেগুলোতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ ছিলো সেগুলোর কয়েকটা নি¤œরূপ-
এক. আ’লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু আল্লাহ্ তা‘আলা ও রসূলে করীমের শানে এমন সব শব্দ ব্যবহার করাকে বেয়াদবী ও ঈমান-বিধ্বংসী বলে ঘোষণা করলেন, যেগুলোকে এক শ্রেণীর লোক সঠিক বলে চালিয়ে দিতে চায়; অথচ সেগুলো আল্লাহ্ ও রসূলের শানে বাস্তবিকপক্ষে বেয়াদবীই। এ ধরনের শব্দাবলী মৌং ক্বাসেম নানূতভীর ‘তাহযীরুন্নাস’-এ, মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর ‘হিফযুল ঈমান’-এ, মৌং খলীল আহমদ আম্বেঠভীর ‘বারাহীনে ক্বাত্বি‘আয়’, মৌং ইসমাঈল দেহলভীর ‘তাক্বভিয়াতুল ঈমান’ ও ‘সেরাত্বে মুস্তাক্বীম’-এ, মৌং মাহমূদ হাসানের ‘আল-জাহদুল মুক্বিল্ল’-ইত্যাদিতে মওজূদ রয়েছে। এসব পুস্তুকের লেখক ও অন্ধ সমর্থকগণ তাদের বক্তব্যগুলোর মর্মার্থ ভিন্নভাবে দেখালেও আ’লা হযরত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, যেহেতু পুস্তকগুলো উর্দু ভাষায় লিখিত এবং সেগুলোর ভাষাও দুর্বোধ্য নয়, সেহেতু উর্দু ভাষীগণ সেগুলোর যেই মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন, তাই বিবেচ্য হবে, শরীয়তমতে হুকুমও সেভাবে দেওয়া হবে।
দুই. আ’লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু বলেছেন, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যে গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য ক্বোরআন ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো যথার্থভাবে বর্ণনা করা অপরিহার্য, যাতে হুযূর-ই আক্রামের মহান ব্যক্তিত্ব বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় আর মুসলমানদের অন্তরগুলোতে হুযূর-ই আক্রামের মহত্ব ও ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু দেওবন্দী মৌলভীগণ সেগুলোকে প্রচার করার ক্ষেত্রে তথাকথিত সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেন অর্থাৎ সেগুলো যথাযথভাবে বর্ণনা করা যাবে না, কারণ তাতে নাকি লোকেরা সীমাতিক্রম করে বসবে; অথচ নবীর শান-মান গোপন করা কিংবা বিকৃত করা জঘন্যতম অপরাধ ও মারাত্মক গুনাহ্।
তিন. আ’লা হযরত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাহফিল-মজলিসগুলোর আয়োজন ও তাতে ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে অংশগ্রহণ করাকে জায়েয এবং মুস্তাহ্সান (মুস্তাহাব) মনে করেন, পক্ষান্তরে দেওবন্দের আলিমগণ সেগুলোর বিপক্ষে ফাত্ওয়াবাজি করেন।
চার.আ’লা হযরতের মতে, মীলাদ-মাহফিলগুলোতে ক্বিয়াম করাকে মুস্তাহাব, পক্ষান্তরে দেওবন্দী আলিমগণ সেটাকে বিদ্‘আত-ই সাইয়্যেআহ্ বলে বিশ্বাস করতেন।
পাঁচ. আ’লা হযরত বুযুর্গানে দ্বীনের ওরস-ফাতিহাকে শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ড থেকে মুক্ত থাকার শর্তে জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত করেন, আর ওলামা-ই দেওবন্দ এটাকে নির্বিচারে না-জায়েয বলে ফাত্ওয়া দিয়ে বসেন।
ছয়. ফাতিহাখানির নিয়মকে, শরীয়তবিরোধী কর্মকান্ড থেকে মুক্ত থাকার শর্তে আ’লা হযরত জায়েয বলেছেন, কিন্তু এটাকেও দেওবন্দী মৌলভীরা বিদ্‘আত ও না-জায়েয বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন।
মোটকথা, এ ধরনের আরো বহু মতবিরোধ ছিলো। যেমন- ‘ইমকানে কিয্ব’ (আল্লাহর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব কিনা), ‘ইমতিনা-‘ঊন নযীর’ (নবী করীমের মতো অন্য কেউ হতে পারে কিনা), ‘হাক্বীক্বতে খাতেমিয়াত’ (নবী করীমের পরে অন্য কোন নবী আসা সম্ভব কিনা), ‘ইলমে গায়ব’ (নবী করীম অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন কিনা), ‘হাযির-নাযির’ (নবী করীম রওযা পাকে রয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থীকে দেখেন ও প্রয়োজনে তার সাহায্য করার জন্য হাযির হতে পারেন কিনা), নূর ও বশর (হুযূর-ই আক্রামের সত্তা মুবারকে নূরানিয়াত ও বশরিয়াতের সমন্বয় সম্ভব কিনা) কবর-যিয়ারত, নবী করীম ও আল্লাহ্র ওলীগণের খোদাপ্রদত্ত ক্ষমতার সাহায্য প্রার্থনার বিধান, মৃতদের শ্রবণক্ষমতা ইত্যাদি। ওলামা-ই দেওবন্দের মুর্শিদ-ই ত্বরীক্বত হাজী ইমদাদ উল্লাহ্ মুহাজির-ই মক্কী প্রায় সব বিষয়ে আ’লা হযরতের ধ্যান-ধারণা ও অভিমতগুলোর সাথে একমত ছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ‘ফয়সালা-ই হাফ্ত মাসআলা’ নামের একটি পুস্তিকাও প্রণয়ন করে গেছেন। কিন্ত দেওবন্দী আলিমগণ তাঁর কথাগুলো মানেননি। এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাাতে আ’লা হযরত ও ওলামা-ই দেওবন্দের মতবিরোধ ছিলো, তা ছিলো হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিষয়। দেওবন্দীগণ দলগতভাবে হিন্দুদের সাথে ঐক্য করে একসাথে কাজ করার পক্ষে। (কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত)। এদিকে আ’লা হযরত এভাবে একসাথে করাকে শরীয়ত মতে মন্দ ও যুক্তিগতভাবে ক্ষতিকর ও মারাত্মক বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ক্ষমতাসীন (ইংরেজগণ) ও সংখ্যা গরিষ্ঠ (হিন্দু)দের সাথে ঐক্য গঠন প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকারক ছিলো। কিন্তু দেওবন্দী আলিমগণ তাঁর সাথে একমত হননি, বরং তাদের কর্মকান্ড এর বিপরীত ছিলো। আ’লা হযরত তাঁর অভিমতের পক্ষে দশটি অকাট্য পুস্তক প্রণয়ন করেনঃ ১. মুনীরুল আয়ন, ২. আযকাল হিলাল, ৩. সুহবানুস্ সুব্বূহ, ৪. সুবাহানুল ক্বুদ্দূস, ৫. আল-মু’তামাদুল মুস্তানাদ, ৬. আল-ক্বুতূফুদ্ দা-নিয়্যাহ্, ৭. আম্বা-উল মোস্তফা, ৮. আল-জুয্উল মুহাইয়্যা, ৯. ইক্বামাতুল ক্বিয়ামাহ্ এবং ১০. হুসামুল হেরমাঈন।
দেওবন্দী আলিমগণ ছাড়াও আ’লা হযরতের জীবদ্দশায় নি¤œলিখিত ফিৎনাগুলো বিরাজিত ছিলো-
১. আহলে হাদীস, ২. আহলে ক্বোরআন, ৩. ওলামা-ই নাদ্ওয়াতুল ওলামা ও ৪. আলীগড়ের বুদ্ধিজীবীগণ। তাদের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার অনেকগুলোকে আ’লা হযরত চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ‘আহলে হাদীস’ তাক্বলীদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললো। তারা নিজেরা ইজতিহাদ করতে পারে বলে দাবী করলো, তারা মাযহাবের চার ইমাম, ফিক্বহ্শাস্ত্র ও মুক্বাল্লিদের বিপক্ষে অশালীন মন্তব্য করতে আরম্ভ করলো। ভারতীয় আহলে হাদীসের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে মৌং ইসমাঈল দেহলভী, মৌং নযীর হোসাঈন দেহলভী, মৌলভী সানা উল্লাহ্ অমৃতস্বরী এবং নবাব সিদ্দীক্ব হাসান খান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আ’লা হযরত আহলে হাদীসের ‘মুজতাহিদ হওয়া’র দাবীকে মুর্খতা বলে প্রমাণ করলেন। সর্বোপরি এটাকে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যে ফাটল ধরানোর নামান্তর বলে আখ্যায়িত করলেন। আ’লা হযরত আহলে হাদীস, মাযহাব বিরোধীদের বিরুদ্ধে যে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন, তা আজ সর্বজনবিদিত। এমনকি দেওবন্দী আলিমদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (পেশোয়ারী) বলেছেন, ‘‘যদি আহমদ রেযা না হতেন, তবে হিন্দুস্তান থেকে হানাফিয়াত (হানাফী মাযহাব) খতম হয়ে যেতো।’’
এরপর আহলে ক্বোরআন, আরো এক কদম এগিয়ে গেলো। ‘আহলে হাদীস’ ফিক্বহ্ শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো, আর এরা হাদীস শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো। তারা বললো, ‘‘দ্বীনী মাসাইল জানা ও বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন নেই, ক্বোরআনই যথেষ্ট।’’ এ অশুভ আন্দোলনের গোড়ার দিকে মৌং আবদুল্লাহ্ চাকড়ালভীর নাম আসে। সে ক্বোরআন-ই করীম ও ‘হাদীসে মুতাওয়াতির’ অনুসারে আমল করাকেই অপরিহার্য সাব্যস্ত করে চাইলো। তারপর মৌলভী আসলাম জীরাজুরী ও গোলাম আহমদ পারভেয আসলো। তারাও অনেক নতুন নতুন গোমরাহী আবিস্কার করলো। মৌং আবদুল্লাহ্ চাকড়ালভী আ’লা হযরতের সমসাময়িক ছিলো। আ’লা হযরত নিজের গবেষণা ও অকাট্য লেখনী দ্বারা তাদের স্বরূপও উন্মোচিত করলেন।
স্যার সাইয়্যেদ আহমদ খান আলীগড়ীও আ’লা হযরতের একই যুগের ছিলেন। বুনিয়াদীভাবে তিনিও মুক্বাল্লিদ ছিলেন। তারপর তার ধ্যান-ধারণায় অনেক পরিবর্তন আসলো। তিনি যেসব চিন্তা ও ধারণা পেশ করলেন। সেগুলোর শুধু আ’লা হযরত বিরোধী ছিলেন না; বরং দেওবন্দী আলিমগণও ওইগুলোর বিরোধিতা করেছিলেন। স্যার সাইয়্যেদ পশ্চিমা সভ্যতাকে গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন। আ’লা হযরত তার চিন্তাধারাকেও ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণ করলেন। এ প্রসঙ্গে আ’লা হযরত নি¤œলিখিত কিতাবগুলো প্রণয়ন করলেনঃ১. লুম্‘আতুত দ্বোহা ফী ‘ই’ফা-ইল লোহা, ২. তামহীদ-ই ঈমান বিআ-য়া-তিল ক্বোরআন, ৩. সামসাম-ই হাদীদ।
মাওলানা শিবলী নো’মানী স্যার সৈয়্যদ আহমদের সমসাময়িক ও সাথী ছিলেন। তিনি আলীগড় কলেজে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক ও ইসলামের মৌলিক জ্ঞানগত বিষয়াদির প্রতি অনীহা লক্ষ্য করলেন। সুতরাং তিনি লক্ষেèৗতে ‘নাদ্ওয়াতুল ওলামা’ নামে একটি নতুন শিক্ষা নিকেতন (পাঠশালা) কায়েম করলেন। প্রথম দিকে ‘নাদ্ওয়াতুল ওলামা’র মাহফিল-মজলিসে (১৮৯৪ খি. অনুষ্ঠিত) আ’লা হযরত আমন্ত্রিত হয়ে শরীক হন, এমনকি আ’লা হযরতকে নাদওয়ার নেসাব কমিটির সদস্য রাখা হয়; কিন্তু পরবর্তীতে যখন ‘নাদ্ওয়াতুল ওলামা’য় প্রত্যেক সম্প্রদায় (চিন্তাধারা)-এর লোকজন শরীক হতে লাগলো, নাদওয়ার পরিচালকগণও সাহায্যের জন্য ইংরেজ ও ইংরেজী হুকূমত (ব্রিটিশ সরকার)-এর দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলো, তখন আ’লা হযরত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। তাঁর মতে, যে কোন প্রতিষ্ঠান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য সবার সমমনা হওয়া অপরিহার্য (পূর্বশর্ত)। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকলে ভাল ফল আশা করা যায়না। মোটকথা, ‘নাদ্ওয়াতুল ওলামা’ ইতিহাস, সিয়র ও সাহিত্যে দক্ষ লোক তৈরী করতে সক্ষম হলেও ধর্মীয় মাসাইলের সঠিক গবেষক, দার্শনিক ও যুক্তিবিদ তৈরি করতে পারেনি। আ’লা হযরত ‘নাদ্ওয়াতুল ওলামা’র কর্মপদ্ধতির বিরোধিতা করে নি¤œলিখিত গবেষণাধর্মী কিতাবাদি প্রণয়ন করেন-
১. ফাতাওয়া আল-হারামাঈন, ২. ফাতাওয়া আল ক্বুদ্ওয়াহ্, ৩. সুয়ূফুল আন্ওয়াহ্ আলা যামা-ইমিন নাদ্ওয়াহ্, ৪. মাআলুল আবরার ওয়া আ-লা-মুল আশরার এবং ৫. সাওয়ালাত-ই ওলামা ওয়া জাওয়াবাত-ই নাদ্ওয়াতুল ওলামা।
আ’লা হযরতের যুগে ‘আহমদী জমা‘আত’ (ক্বাদিয়ানী)ও আত্মপ্রকাশ করলো। এর প্রবর্তক হলো মির্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানী। সে ১২৫০হি./১৮৩৫ খ্রি. আ’লা হযরতের শুভ জন্মের প্রায় বিশ বছর পূর্বে ক্বাদিয়ান (পূর্ব পাঞ্জাব, ভারত)-এ জন্মগ্রহণ করেছিলো। সে নুবূয়তের দাবীদার হয়ে বসলো। ১৮৮২ খ্রি. সে তার দাবীটার সূচনা করেছিলো। দীর্ঘদিন পর ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম হাকীম নুরুদ্দীন তার হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেছিলো। এরই মাধ্যমে অখন্ড ভারতে আরেকটা নতুন ফিৎনা শুরু হলো। মির্যা ক্বাদিয়ানী জোরে শোরে ইংরেজদের সমর্থন করতে লাগলো; জিহাদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করলো। ভন্ড নুবূয়তের দাবী করার ফলে গোলাম আহমদের প্রতি ইংরেজ ও হিন্দু সম্প্রদায় উভয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলো; ইংরেজগণ এজন্য যে, ভারতে ওই সময় তারা গোলাম আহমদকে তাদের সমর্থক হিসেবে পেয়েছিলো, যখন তাদের এমন সমর্থকের প্রয়োজন ছিলো। হিন্দুরা এজন্য সন্তুষ্ট ছিলো যে, কাদিয়ানীদের নিকট মক্কা শরীফের পরিবর্তে ‘কাদিয়ান’ তাদের ধর্মের কেন্দ্রভূমি স্থির হয়েছে। কারণ, তাদের অভিযোগ ছিলো যে, মুসলমানগণ থাকেন ভারতে, কিন্তু কথা বলেন মক্কা মুকাররামার।
আ’লা হযরত এ নতুন ফিৎনার দিকে তাৎক্ষণিকভাবে মনোনিবেশ করলেন। একাধিক ফাত্ওয়া তার বিরুদ্ধে প্রণয়ন করলেন। তাকে কাফির সাব্যস্ত করলেন। নি¤œলিখিত পুস্তকগুলোতে তিনি ক্বাদিয়ানীর খন্ডন ও পিছু ধাওয়া করেছেন- ১. আস্সা-রিমুর রাব্বানী ‘আলা ইসরাফিল ক্বাদিয়ানী, ২. জাযাল্লাহু আদুওভাহ্ বিইবা-ইহী খতমিন্ নুবূয়ত, ৩. আস্ সূ-উল ‘ইক্বাব ‘আলাল মসীহিল কায্যাব, ৪. ক্বাহ্রুদ্ দাইয়্যান ‘আলা মুরতাদ্দিল ক্বাদিয়ান এবং ৫. আল-মুবীন খাতামুন নাবিয়্যীন।
আ’লা হযরত বেরলভীর এসব প্রচেষ্টাকে সামনে রেখে মৌলভী মুহাম্মদ যিয়াউদ্দীন তার ‘মুসাদ্দাস’ (ছয় পংক্তি বিশিষ্ট কবিতা)-এ স্পষ্ট করেছেন-
وه احمد رضا زمانے ميں يكتا
اسى سے دبا قاديانى كا فتنه
অর্থ: ওই (ইমাম) আহমদ রেযা যুগের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরই প্রচেষ্টায় গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর ফিৎনা দমিত হয়েছে।
আ’লা হযরত বেরলভী ভিন্ন ভিন্ন আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে ওইসব আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলেছেন। আর ক্রমশ: তাদের কর্মপদ্ধদিতে পরিবর্তন আসতেও দেখা গেছে। যেমন-
এক. যারা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শুধু অনুসরণের উপর জোর দিতো, ইশক্বে রসূল ও মুহাব্বতে রসূলের কথা বলতোনা, তারা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসাকে ইসলামী মিল্লাতের প্রাণ মনে করতে লাগলো।
২. যারা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাহফিলগুলোর সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলো, বিশেষ করে ১২ রবিউল আউয়াল-এর; সেটাকে বিদ্‘আত মনে করতো, তারা ওই ধরনের মাহফিলে শরীক হতে লাগলো। ‘সীরাতুন্নবী’ নামে তারা সভা-মজলিস আয়োজন করতে আরম্ভ করলো।
তিন. যারা ওলীগণের ওরস অনুষ্ঠানের বিপক্ষে ছিলো, বিশেষ করে তাঁদের ভেসাল (ওফাত)-এর দিনে, তারা ওরসগুলোতে শরীক হতে লাগলো, সালানা ইজতিমা’র নামে ওরস করতে আরম্ভ করলো।
চার. যারা ঈসালে সাওয়াব ও ক্বোরআনখানিকে বিদ্‘আত মনে করতো, তারা এখন ক্বোরআনখানি করতে আরম্ভ করেছে।
পাঁচ. যারা ওরস ও ফাতিহার খাবার খাওয়াকে না-জায়েয মনে করতো, এখন তারা ওইসব খাবার খেতে আরম্ভ করেছে।
ছয়. যারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিরুদ্ধে আ’লা হযরত বেরলভী অবস্থানকে ভালো দৃষ্টিতে দেখতো না, তারাও পরবর্তীতে আ’লা হযরতের সাথে একমত হয়ে গেছেন।
এভাবে অনেক বিষয়ে আ’লা হযরতের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভারতের মুসলমানদের উপর আ’লা হযরতের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; তা উপেক্ষা করার মতো নয়।
আ’লা হযরতের রাজনৈতিক আন্দোলন
ইংরেজগণ পাক-ভারত উপমহাদেশে এসেছিলো ব্যবসায়ী হিসেবে; কিন্তু এরপর তারা এখানকার রাজনৈতিক অবস্থা- দির সুযোগ নিয়ে এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লো। ক্রমশ: তারা পুরো ভারতবর্ষের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করলো। এখানকার লোকেরা ইংরেজদের ক্ষমতাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিলো, যা হঠাৎ করে ১৮৫৭ ইংরেজিতে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা (সিপাহী বিপ্লব) হিসেবে প্রকাশ পেয়েছিলো। এটা জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিলো।
এটা পাক-ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর ছিলো। বিদেশী ক্ষমতার মূলোৎপাটনের জন্য আজাদীর সর্বশেষ যুদ্ধ করা হলো এ বছর; কিন্তু এ উপমহাদেশের জনগণের এ যুদ্ধে পরাজয় হলো। আর ইংরেজগণ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও সমর্থনকারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিলো। এ পরাজয়ের অশুভ প্রভাব জনগণের সব ক্ষেত্রে পড়েছিলো। কিন্তু আযাদী লাভের প্রেরণাকে তারা নির্মূল করতে পারেনি। এ দমিত আগুন কিছুদিন পর আবারো জ্বলে উঠেছিলো।
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের প্রায় ২৫ বছর পর, যখন ইংরেজদের রোষানল কিছুটা স্তমিত হয়েছিলো, ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডিফ্রেনের ইঙ্গিতে ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। তখন আ’লা হযরতের বয়স ছিলো প্রায় ২৮ বছর। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, ভারতীয়দের দাবী দাওয়া সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ সরকারের সামনে পেশ করা যাবে। প্রত্যেক ধর্মের লোকেরা এতে শরীক ছিলো। মুসলমানগণ তাতে শরীক হবেন কিনা ফাত্ওয়া নেওয়া হলো। কিছু সংখ্যক মুসলমান তাতে অংশগ্রহণের পক্ষে ফাত্ওয়া দিলেন। যেমন-মৌং রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং মৌং মাহমূদ হাসান দেওবন্দী বিগত ১৮৮৮খ্রি. এ ধরনের ফাত্ওয়া দিলেন। কিন্তু যখন আ’লা হযরতের নিকট ফাত্ওয়া চাওয়া হলো, তখন তিনি তাতে অংশগ্রহণের জন্য এমন সব শর্ত আরোপ করলেন, যেগুলো থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন দক্ষ রাজনীতিবিদও ছিলেন; তাঁর মধ্যে অনন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিলো। এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অদূর ভবিষ্যতে আসবে এমন অনেক বিপদ আগেভাগে অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন। তিনি ফাত্ওয়া দিলেন-
‘‘মুসলমানদের কর্মব্যবস্থাপক, আলোকিত পরামর্শক, গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন, পরিণামদর্শী এবং সূক্ষ্ম গবেষকদের অত্যন্ত গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা করা দরকার যে, এ’তে (কংগ্রেসে অংশগ্রহণ) বর্তমানে ও ভবিষ্যতে (পরিণতিতে) ইসলাম ও মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি আছে কিনা।’’
আ’লা হযরত কংগ্রেসে মুসলমানদের অংশ গ্রহণে সমূহ বিপদের আশঙ্কা অনুধাবন করেন, ১৮৮৫ সালে, ‘জমা‘আত-ই রেযা-ই মোস্তফা’ নামে একটি সংস্থা কায়েম করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। এটা প্রতিষ্ঠালাভ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও সমাধা করেছিলো। এর বুনিয়াদী উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের সংগঠিত করা ও তাঁদের অবস্থার সংস্কার করা। ওদিকে ১২২১ হি./১৯০৩খ্রি. ‘নায্যারাতুল মা‘আ-রিফ’ নামে একটি সংস্থা কায়েম হলো, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মৌং মাহমূদ হাসান, হেকীম আজমাল খান এবং নবাব ওকারুল মুলক প্রমুখ। মৌং ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী প্রাণসঞ্চারক ছিলেন। তিনি ‘জমিয়তুল আনসার’-এর মহা ব্যবস্থাপক ছিলেন।
‘নাযযারাতুল মা‘আরিফ’ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরই ১৯০৫খি. ‘রেশমী রুমাল আন্দোলন’ শুরু হলো। সেটার উদ্দেশ্য ছিলো ‘উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করে বিদেশী রাজত্ব খতম করা।’ কিন্তু ১৯০৬খ্রি. এ ষড়যন্ত্র ফাঁশ হয়ে গেলো। মৌং মাহমূদ হাসান ও মৌং হোসাঈন আহমদ গ্রেফতার হন। ‘রেশমী রুমাল আন্দোলন’ চলাকালে (১৯০৬খ্রি.) ‘অল-ইন্ডিয়া মুসলিমলীগ’ কায়েম হলো। এর উদ্দেশ্যও মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিলো। এরপর এ লীগও বহু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। এরই প্রচেষ্টার ফলে উপমহাদেশে আরেকটি নতুন রাষ্ট্র (পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর ১৯১২খ্রি. ত্রিপলী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ফলশ্রুতিতে ত্রিপলী ইটালীর দখলে চলে গেলো। তারপর বলকান যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং তুর্কিরা পরাজিত হলো। এরপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলো। এ যুদ্ধে ইংরেজদের পাক-ভারতের লোকদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিলো। তারা স্বরাজ আন্দোলনের ঘোষণা দিলো। হিন্দু ও মুসলমান সবাই এ আশায় তাদের সাহায্য করলো যে, যুদ্ধের পর স্বাধীনতা মিলবে। হিন্দুদের নেতা মি.গান্ধী আর মুসলমানদের নেতা মুহাম্মদ আলী জওহার হিন্দু ও মুসলমানদেরকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করলেন। এ যুদ্ধে ইংল্যান্ড, রাশিয়া ফ্রান্স ওসমানিয়া সালতানাত-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো। অনুরূপ ভারতীয় মুসলমানদেরকে নিজেদের ভাইদের রক্ত প্রবাহিত করার জন্য সেনাবাহিনীতে ভর্তি করানো হচ্ছিলো।
মোটকথা, যখন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হলো। কিন্তু ইংরেজগণ তাদের ওয়াদা থেকে ফিরে গেলো। আর স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবর্তে ওসমানিয়া সালতানাতের বিভিন্ন অংশ দখল করতে থাকে। এতে উপমহাদেশের মুসলমানগণ ক্ষোভে ফেটে পড়লো। ১৯১৯খ্রি. খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হলো, যার উদ্দেশ্য ওসমানিয়া সালতানাৎকে হিফাযত করা ও সাহায্য করা বলে দাবী করা হলো। এ আন্দোলনে হিন্দু নেতা গান্ধীও অংশগ্রহণ করলো এবং তাকে এ আন্দোলনের প্রধান নেতা স্থির করা হলো। এর পরবর্তী বছরেই ১৯২০খ্রি. অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হলো। আবেগের এমন সয়লাব প্রবাহিত হলো যে, সবাই নির্দ্বিধায় গান্ধীর ইঙ্গিতে চলতে লাগলো। মৌং মাহমূদ হাসান তখন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি জমিয়তুল ওলামা-ই হিন্দের সভায় (দিল্লী ১৯২০খ্রি.) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন, ‘‘ইংরেজদের সাথে অসহযোগ ফরয। আর খিলাফতের হিফাযত করতে হিন্দুদের অংশগ্রহণ কৃতজ্ঞতার উপযোগী। ‘অসহযোগ আন্দোলন’-এর সাথে সাথে শুরু হলো ‘দেশত্যাগ আন্দোলন’। তারপর ‘গাভী যবেহ্ বর্জন আন্দোলন’, ‘খদ্দর আন্দোলন’ ও ‘পশু বর্জন আন্দোলন’ ইত্যাদিও চলতে লাগলো।
আ’লা হযরত উপরিউক্ত রাজনৈতিক অবস্থাদি ও ঘটনাবলী অতি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। আর কতিপয় পুস্তক ও ফাত্ওয়ায় তাঁর নিজস্ব অভিমত ও ধ্যান ধারণা প্রকাশ করেছেন। তিনি একথা প্রমাণ করেছেন যে, ‘খিলাফত আন্দোলন’-এর উদ্দেশ্য ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি ছিলোনা; বরং নেপথ্যে ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রচেষ্টাই ছিলো; যাতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো, তারাই এ আন্দোলনে উপকৃত হতো।
সুতরাং অসহযোগ আন্দোনের প্রতি আ’লা হযরতের সন্দেহগুলোর সত্যায়ন হয়। আর ‘শুদ্ধি সংগঠনের আন্দোলন’ (১৯২৩খ্রি.)-এ সন্দেহগুলো স্পষ্টভাবে সামনে এসে যায়, যখন ১৯১৯খ্রি. থেকে ১৯২১খ্রি. পর্যন্ত ভ্রাতৃত্বের দোহাই দাতারা মুসলমানদেরকে মুরতাদ্দ বানানো ও হিন্দু সভ্যতাকে গ্রহণের উপর বাধ্য করার জন্য এক ব্যাপকতর আন্দোলন চালিয়েছিলেন।
আ’লা হযরতের ধারণায় প্রত্যেক কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব রাখা হারাম। অবশ্য লেনদেন করা মূল কাফিরদের সাথে জায়েয। আ’লা হযরতের মতে, এসব ক’টি আন্দোলন মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে; পক্ষান্তরে, হিন্দুদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছে। তিনি লিখেন-
‘শত্রু তার শত্রুর জন্য তিনটি কথা চায়-
১. প্রথমে তার মৃত্যু, যাতে ঝগড়াই খতম হয়।
২. এটা না হলে তার দেশান্তর, যাতে নিজের কাছে না থাকে,
৩. এটাও না হলে শত্রুর মোকাবেলায় ঢাল হয়ে থাকুক।
বিশ্বযুদ্ধে মুসলমানদেরকে ঠেলে দিয়ে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য হাসিল করা তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। এভাবে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। স্বদেশ ত্যাগ আন্দোলন চালিয়েও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলো হিন্দু নেতারা। আর অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে তারা তৃতীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলো। তাছাড়া, এ তিনটি উদ্দেশ্যই তারা ভারত বিভক্তির (১৯৪৭খ্রি.) সময় চরিতার্থ করেছিলো। হত্যাযজ্ঞের বাজার উত্তপ্ত করা হয়েছিলো। মুসলমানদেরকে ভারত ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিলো। যেসব মুসলমান ভারতে র’য়ে গিয়েছিলেন, তাদের জন্য জীবন ধারণের পথ বন্ধ করে দিয়েছিলো। আ’লা হযরত হিন্দু-মুসলিম বন্ধুত্বকে যে আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখেছেন, ড. ইকবালও একই সন্দেহের চোখে দেখেছেন; অথচ তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতি আহ্বানকারী ছিলেন। তিনি (আল্লামা ইকবাল) পরবর্তীতে নি¤œলিখিত আশঙ্কাগুলো প্রকাশ করেছিলেন-
১. গ্রহণযোগ্য হিন্দু-মুসলিম চুক্তি ছাড়া নিছক ইংরেজদের প্রতি শত্রুতার ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে প্রস্তর স্থাপন সম্ভবপর ছিলোনা।
২. এ আশঙ্কাও ছিলো যে, এমন মেলামেশা ও মুসলমানদের সরলতার সুবাদে জাতীয় ঐক্যের আহ্বায়ক তাদের পৃথক ধর্মীয় অবস্থানকে নিঃশেষ করে দেবে।
যেই আশঙ্কার প্রকাশ আল্লামা ইকবাল অনেক পরে করেছেন, আ’লা হযরত বেরলভী ওইসব আশঙ্কার দিকে মুসলিম মিল্লাতকে অনেক আগেই অবহিত করেছিলেন। তিনি কারো সমালোচনার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাঁর আশঙ্কাগুলো প্রকাশ করেছিলেন। আ’লা হযরতের ধারণা ছিলো যে, সমস্ত সম্প্রদায় মুসলমানদের শত্রু- চাই তারা ইংরেজ হোক অথবা ইহুদী হোক কিংবা কাফির ও মুশরিকগণ হোক, অথবা হোক তারকাপূজারী কিংবা অগ্নি পূজারী।
আ’লা হযরত জাতি গঠনের পক্ষে ছিলেন। এজন্য তিনি যে নিয়ম-নীতি নির্দ্ধারণ করেছিলেন। তাঁর পরে তার সাহেবযাদাগণ, খলীফাগণ, ছাত্রগণ এবং অনুসারীগণ সেগুলোর অনুসরণ করে মুসলিম মিল্লাতকে পরিচালনা করেছেন। ১৯৪০ খ্রি.পর দল হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সহযোগিতা করেছেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যানারস কনফােেন্স পাকিস্তানের সমর্থনে সর্বসর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ফলে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে ও প্রচেষ্টায় আলিমদের সমর্থনে পাকিস্তান কায়েম হয়।

